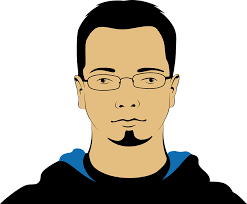

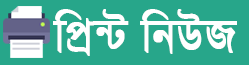
কালনেত্র ডেস্ক
ক্লিনটেক মানে হল এমন সব জিনিস, পরিষেবা আর পদ্ধতি—যেগুলি পরিবেশের ক্ষতি কমায়। এগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিকমত ব্যবহার করে, শক্তি বাঁচায় ও বর্জ্য কমায়। আর পরিবেশের ওপর খারাপ প্রভাব কমিয়ে আমাদের অর্থনীতিরও উপকার করে।
নবায়নযোগ্য শক্তি, শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, পানি পরিষ্কার করার সিস্টেম, বর্জ্য ম্যানেজমেন্ট, পরিবেশবান্ধব গাড়ি আর গ্রিন বিল্ডিং—এইসব ক্লিনটেকের আওতায় পড়ে।
.
ক্লিনটেকের শুরু যেভাবে
ক্লিনটেক খুব নতুন কিছু না। কিন্তু আলাদা একটা খাত হিসেবে যেভাবে এখন গড়ে উঠেছে, সেটা ঘটেছে গত কয়েক দশকে।
১৯৭০-এর দশকে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে OPEC তেল রপ্তানি বন্ধ করে দিলে বিশ্বজুড়ে তীব্র তেল সংকট দেখা দেয়। হঠাৎ তেলের দাম বেড়ে যায়, এবং উন্নত দেশগুলি জ্বালানির ওপর নির্ভরতার ঝুঁকি বুঝতে পারে। এই সংকটই প্রথমবারের মত বিকল্প শক্তির দিকে দৃষ্টি ফেরায় বিশ্বকে। সৌর, বায়ু, জিওথার্মাল ও হাইড্রো শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। যদিও প্রযুক্তি তখনও অপরিণত ছিল, তবুও সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন শক্তির উৎস খুঁজতে সক্রিয় হয়। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ক্লিনটেকের প্রাথমিক ধারণা—শুধু বিকল্প শক্তি নয়, বরং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়।
১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে পরিবেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা অনেক বেড়ে যায়। একের পর এক বড় পরিবেশগত বিপর্যয়—যেমন ১৯৮৪ সালের ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, ১৯৮৬ সালের চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা এবং ওজোন স্তর ক্ষয়ের মত ঘটনা মানুষকে নাড়া দেয়। এইসব ঘটনায় মানুষ বুঝতে পারে, শিল্প ও প্রযুক্তি যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তার ভয়াবহ ফল হতে পারে পরিবেশ ও মানুষের জীবনে। তখন থেকেই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে নজর বাড়ে। সরকার, বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ—সবাই টেকসই সমাধান খুঁজতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই প্রবণতা ক্লিনটেক ধারণাকে আরও শক্ত ভিত দেয়।
২০০০-এর দশকে ক্লিনটেক খাতে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেড়ে যায়। তখন একে বলা হয় “ক্লিনটেক ১.০”। প্রযুক্তি তখনও খুব ব্যয়বহুল ছিল, আর বাজার ছিল অপরিণত। ফলে বেশিরভাগ উদ্যোগ টেকেনি এবং বিনিয়োগকারীরা হতাশ হন।
এরপর ২০১০-এর দশকে শুরু হয় ক্লিনটেক ২.০। এই পর্যায়ে প্রযুক্তির খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে, আর কার্যকারিতাও অনেক বেড়ে যায়। সৌরশক্তি, ব্যাটারি স্টোরেজ, বৈদ্যুতিক যানবাহন (EV) ও স্মার্ট গ্রিডের মত প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসে। একইসাথে প্যারিস চুক্তির মত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও সরকারিভাবে পরিবেশবান্ধব নীতির প্রসারে এই খাতে নতুন করে বিনিয়োগ বাড়ে। ফলে ক্লিনটেক ২.০ বাস্তবসম্মত, লাভজনক ও টেকসই একটি ধাপে পরিণত হয়, যা এখনও চলমান এবং ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।
.
ক্লিনটেক ও ক্লাইমেটটেক এর পার্থক্য
ক্লিনটেক (Cleantech) এর মত আরেকটি ঘনিষ্ঠ এবং প্রায়শই সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয় এমন একটি ধারণা হল ক্লাইমেট টেক (Climate Tech)। দুটিই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে বলে অনেকেই ভাবেন, এগুলি এক। এই বিভ্রান্তি তৈরি হয় কারণ দুটি ক্ষেত্রেই টেকনোলজির মাধ্যমে পরিবেশের উপকার করার চেষ্টা চলে। কিন্তু ভালভাবে দেখলে বোঝা যায়, ক্লিনটেক যেখানে পরিবেশের ওপর সামগ্রিক চাপ কমাতে কাজ করে (যেমন—পানি বিশুদ্ধকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), সেখানে ক্লাইমেট টেক মূলত কাজ করে জলবায়ু পরিবর্তন ও কার্বন নিঃসরণ মোকাবিলায়।
ধরুন, কোনো কোম্পানি পানি পরিশোধনের একটা প্রযুক্তি বানাচ্ছে, যেটা কার্বন নিঃসরণ না কমালেও নদীর পানি পরিষ্কার রাখে—এটা শুধুই ক্লিনটেক। আবার কোনো টেকনোলজি যদি বাতাস থেকে কার্বন শোষণ করে, সেটা বিশেষভাবে ক্লাইমেট টেক।
সোজা ভাষায়—সব ক্লাইমেট টেক-ই ক্লিনটেকের মধ্যে পড়ে, কিন্তু সব ক্লিনটেক ক্লাইমেট টেক নয়।
ক্লিনটেকের বর্তমান ব্যবহার
এই সময়ে ক্লিনটেক শুধু ভবিষ্যতের পরিকল্পনা না—এখনই আমাদের আশপাশে বাস্তব হয়ে উঠেছে। সৌর প্যানেল, উইন্ড টারবাইন, জিওথারমাল পাওয়ার, স্মার্ট গ্রিড আর শক্তি জমিয়ে রাখার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি—সবই এখন জ্বালানি খাতে সাধারণ চিত্র।
ইলেকট্রিক আর হাইব্রিড গাড়ির বাজার ক্রমেই বাড়ছে, হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল আর পরিবেশবান্ধব পাবলিক ট্রান্সপোর্টও আস্তে আস্তে চালু হচ্ছে। পানির ব্যবস্থাপনায়ও দেখা যাচ্ছে বড় পরিবর্তন—আধুনিক পানি পরিশোধন ব্যবস্থা, বৃষ্টির পানি ধরে রাখার প্রযুক্তি, আর বর্জ্য পানি পুনঃব্যবহার এখন অনেক জায়গায় চালু। একইভাবে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রিসাইক্লিং, কম্পোস্টিং আর বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে।
কৃষিক্ষেত্রে এসেছে প্রিসিশন এগ্রিকালচার, যেখানে কম পানি ও সারেই বেশি ফসল তোলা সম্ভব। সোলার ইরিগেশন পাম্পের ব্যবহার বাড়ায় ডিজেলের প্রয়োজন কমেছে। আর নির্মাণ খাতে ‘গ্রিন বিল্ডিং’ এখন এক নতুন স্ট্যান্ডার্ড—যেখানে টেকসই উপকরণ আর শক্তি সাশ্রয়ী ডিজাইন ব্যবহার হচ্ছে।
বিশ্বের নানা প্রান্তে ক্লিনটেকের সফল উদাহরণ এখন আরও স্পষ্ট:
যুক্তরাষ্ট্রে, টেসলা বৈদ্যুতিক গাড়ি আর ব্যাটারি প্রযুক্তিতে বিপ্লব এনেছে। নেভাদার জেমিনি প্রকল্প সৌর শক্তি ও স্টোরেজ একসাথে যুক্ত করছে। আরও নতুন হচ্ছে DAC (Direct Air Capture) টেকনোলজি, যা বাতাস থেকে কার্বন শোষণ করে।
ইউরোপে, ডেনমার্কের ওরস্টেড অফশোর বায়ুতে ওয়ার্ল্ড লিডার। সুইডেনের নর্থভোল্ট তৈরি করছে টেকসই ব্যাটারি। আর জার্মানির ভাউবান পরিবেশবান্ধব শহর কেমন হওয়া উচিত, তার দারুণ উদাহরণ।
এশিয়ায়, চীন এখন সোলার প্যানেল আর ইলেকট্রিক গাড়ি উৎপাদনের দিক থেকে শীর্ষে। ভারত সোলার স্থাপনে দ্রুত এগোচ্ছে। সিঙ্গাপুর তৈরি করছে NEWater ও ভার্টিকাল ফার্মিংয়ের মত মজাদার নগরভিত্তিক সমাধান।
আফ্রিকায়, কেনিয়া শক্তিশালী জিওথার্মাল গ্রিড গড়ছে আর অফ-গ্রিড সোলার প্রজেক্টে এগিয়ে। মরক্কো বানিয়েছে বিশাল কনসেন্ট্রেটেড সোলার প্ল্যান্ট। দক্ষিণ আফ্রিকাও নবায়নযোগ্য শক্তিতে জোর দিচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ায়, প্রায় প্রতি ছাদে সোলার প্যানেল! সেই সঙ্গে, স্নোয়ি ২.০ হাইড্রো প্রজেক্ট আর হর্নসডেল টেসলা ব্যাটারি পৃথিবীর বড় বড় শক্তি সংরক্ষণ প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম।
চোখে পড়ার মত ব্যাপার হল—ক্লিনটেক এখন শুধু একেকটা খাতের প্রযুক্তি না, বরং এক ধরনের গ্লোবাল ট্রান্সফর্মেশন। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, ছোট উদ্যোগ থেকে বড় কোম্পানি—সবাই ধীরে ধীরে এই দিকেই এগোচ্ছে।
সমালোচনা, চ্যালেঞ্জ ও সামাজিক প্রভাব
ক্লিনটেকের সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু চ্যালেঞ্জও আছে। এর প্রাথমিক খরচ অনেক সময় বেশি হয়। আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নবায়নযোগ্য শক্তির সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়, আর গ্রিডের স্থিতিশীলতাও একটা বড় বিষয়। সোলার প্যানেল ও ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহৃত খনিজ উত্তোলন পরিবেশের ক্ষতি করে। বড় প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ স্থানীয়দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে।
চ্যালেঞ্জ থাকলেও ক্লিনটেকের ভবিষ্যৎ খুবই আশাব্যঞ্জক। AI আর IoT-এর মত প্রযুক্তির সংযোজনে এটি আরও কার্যকর ও সাশ্রয়ী হয়ে উঠবে। উৎপাদন বাড়ার সাথে খরচও কমবে। জলবায়ু সচেতনতা ও টেকসই বিনিয়োগের আগ্রহ বাড়ায় এই খাতে বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতের জ্বালানি মিশ্রণে গ্রিন হাইড্রোজেন, উন্নত পারমাণবিক প্রযুক্তি (SMR), কার্বন ক্যাপচার (CCS) আর উন্নত শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা বড় ভূমিকা রাখবে।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা অনেক। উপকূলীয় এলাকায় বায়ু শক্তি, শহরে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ এবং জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষিতে ক্লিনটেকের ব্যবহার শুরু করা সম্ভব।
দ.ক.সিআর.২৫